সেলিম মোরশেদ যেন বা ব্যক্তিগত আমোদেই পাঠকের সামনে এক দেয়াল তুলে তার গল্পগুলো বলে গেছেন। সম্ভবত চেয়েছেন, পাঠক তাকে আবিষ্কার করুক। লেখক যখন চাইবেন পাঠক তাকে নিজ দায়িত্বে আবিষ্কার করুক তখন দিশাহীন পাঠকের দিকে হাত বাড়ানো উচিত লেখকের। অন্ততপক্ষে আলো জ্বেলে পথ দেখানোর উপলক্ষ তৈরি করতে পারেন লেখক। কিন্তু মনে হয়েছে, সেলিম মোরশেদ পাঠকের দিকে হাত বাড়াননি। এমনকি কোনো আলোও জ্বেলে দেননি যা পাঠককে পথ দেখাবে। ফলে, লেখার গোলকধাঁধায় হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগিয়ে পাঠক তাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে উদ্যম হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাই প্রবল।
সেলিম মোরশেদকে এ কয়েক লাইনে ব্যাখ্যা করে যদি বসে থাকেন তবে আপনার চোখে না-ও পড়তে পারে তার সমস্ত প্রজ্ঞা, বুদ্ধিদীপ্ত বয়ান, তীক্ষ্ন রাজনীতি সচেতনতা, তার বোধ, ন্যারেটিভের ধারাবাহিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উপন্যাস রচনায় নতুন আঙ্গিক দেয়ার চেষ্টা কিংবা হতে পারে আপনি বুঝবেন না শব্দ নিয়ে কী এক প্রবল যুদ্ধে মত্ত তিনি। নানা দিক দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার গল্প ছাপিয়ে আমাকে ভাবিয়েছে উপন্যাসিকা ‘সাপলুডু খেলা’। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিলো মি. নোবডি সিনেমার মতোন ননলিনিয়ার ন্যারেটিভে লেখা। সিনেমাটা আসলে অনেকগুলো গল্প একসাথে বলে আর এত দ্রুততায় গল্প পাল্টে পাল্টে যায় যে দর্শককে সব গল্পের সুতো জোড়া দিতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে হয়। আর যদিও বা গল্পগুলোর সুতো জুড়ে দেয়া যায় তবে সামনে এসে দাঁড়ায় অনেকগুলো স্বতন্ত্র গল্প। সে সব গল্প মিলে আবার এক কেন্দ্রে মিলে তৈরি করে একটি মূল গল্প। মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার গল্পই বলে আসলে সিনেমাটি।
সাপলুডু খেলা সত্যি বলতে ওভাবে কোনো গল্প বলে না। অরৈখিক বয়ানে যেটুকু উঠে আসে এ উপন্যাসিকায় তা বোধ আর উপলব্ধির বয়ান। এর মানে আবার এতে একদমই গল্প নেই তা নয়। গল্প আছে ঢের। সেসব গল্পের শুরুটা ধরিয়ে দিয়ে লেখক পাল্টে ফেলেছেন দৃশ্যপট। কোনটাই সম্পূর্ণ নয়। এমনকি ফেলে আসা দৃশ্যপটে তিনি আর ফেরান নি পাঠককে। এখানে পাঠকের কল্পনার জন্যে বেশ অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। গল্পগুলো পাঠক ভেবে নিতে পারেন নিজের মতো করে। কেউ কেউ বলেন, ছফার পুষ্প, বৃক্ষ ও বিহঙ্গ-ও অরৈখিক বয়ানের বই। এক দিক থেকে এ দাবি মিথ্যে নয়। কিন্তু ছফা বইটিতে যখন ফুলের কথা বলেছেন ফুলের প্রসঙ্গেই থেকেছেন, বৃক্ষ প্রসঙ্গে যখন এসেছেন তখন তা এলোমেলো হলেও অন্য প্রসঙ্গে যান নি। আবার বিহঙ্গের আলাপ যখন করেছেন তখনও সেখানে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। পাঠকের ছফার বক্তব্য ধরতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু ‘সাপলুডু খেলা’ আলাদা বস্তু। পাঠক এখানে কোনো ধারাবাহিক গল্প পাবেন না।
কিন্তু কোন পাঠকদের কথা বলছি আমি। সেলিম মোরশেদের পাঠক কারা? তার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড় করিয়ে দেয়া গল্পকথন বেশিরভাগ পাঠককেই তো ফেরাবে নিরাশায়! এটা কী তিনি সচেতনে করেছেন? তিনি কী নিজেই বেছে নিয়েছেন পাঠকদের? সযত্নে ছেঁকে নিয়ে কেবল সেসব পাঠককেই চেয়েছেন যারা পরিশ্রমী; পড়াটা যাদের কাছে আনন্দদায়ী নয় কেবল, অস্তিত্বেরও অংশ? জানি না ঠিক বললাম কী না, সম্ভবত তিনি তা-ই করেছেন। তার ‘সাপলুডু খেলা’ আমাকে বলে, তিনি সাহিত্য করনেওয়ালাদের পাঠক তৃপ্তির জন্যে লিখে চলার প্রথা ভাঙতে চেয়েছেন। এটা আমার পছন্দ হয়েছে। পাঠককে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছেন বারে বারেই। তিনি সচেতনভাবেই চেয়েছেন পাঠক চিন্তাশীল হয়ে তাকে পড়ুক।
কেন ছোটেন এইসব লেখকেরা, কীসের আশায়? এসবের উত্তরে উপলব্ধিতে আসে এটুকুই যে, তারা আসলে কিছু বলতে চান। এ বলাটুকুই লেখকের আনন্দ। প্রাপ্তি। উচ্ছ্বাস। অর্থকড়ি যশ-খ্যাতি না জুটলেও লেখক এ বলার স্বাধীনতাটা চান। এ স্বাধীনতাটুকু মেনে নিলেই যেন মেলে তার সাতরাজার ধন।
পাঠককে বঞ্চিত করেছেন তার প্রমাণ দিতে গিয়ে সাপলুডু পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি- জুবায়েরের ধর্ম বিশ্বাস বিষয়ক আলাপে পাঠক যখন ডুবে গেছে প্রায় ঠিক তখনই যেন মুচকি হেসে সেলিম মোরশেদ প্রসঙ্গ-দৃশ্যপট বদলে ফেলেন। আবার উল্লেখ করা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখক/গল্পকথক ও তার পরিবারের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালানোর, নীতার সাথে সখ্যতার কথা। নীতা ও গল্পকথকের ভাব ও বোঝাপড়া গাঢ় হয়ে উঠতে না উঠতেই আবারো পাঠককে ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়ান সেলিম মোরশেদ। যেন বলতে চান- অনেক হইছে এখানে, এবার আগে বাড়ো, দেখো সামনে কী আসে!
আবার কিঞ্চি দেমার সাথে ভুটানে গল্পকথকের আনন্দময় ও প্রাণবন্ত আলাপ জমে উঠতে না উঠতেই লেখক আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসেন সলোমনের কাছে। যেন পণ করেছেন কিছুতেই পাঠককে স্বস্তি দেবেন না! এরপর সলোমন বাকি পথ পাঠককে একাই টেনে নেয়। যদিও সলোমন যতটা না এক চরিত্র তার চেয়ে বেশি সে এক প্রতীক আমার কাছে। প্রতীক এমন শ্রেণীর, যারা সবখানেই আছে। এরা একই সাথে সুবিধাভোগী এবং ইন্টেলেকচুয়াল। মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে এরা ভাবে কিন্তু সে কষ্ট ও দুঃখ তারা নিজের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এরা যতটা না সমাজ পরিবর্তনের কর্মী তার চেয়ে বেশি ভাবুক। এরা কিছু চাপিয়েও দেয় না আবার কিছু গ্রহণও করে না। নিজেকে বদলাতে ইচ্ছুক না হয়েও অন্যের রূপান্তর দেখতে মরিয়া। পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে এরা আলুর মতো, সব তরকারিতেই যায়। এটুকু জানি যে, এরা চিন্তার উদ্রেককারী। এ কারণে, ভাবুকের চেয়ে কর্মী আমার পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সলোমন তথা লেখকের উপলব্ধি ও মনন প্রকাশের প্রধান মাধ্যমকে মেনে নিই। নিজেকে প্রবোধ দিই- সবাই কর্মী হয় না, ভাবুকেরও দরকার আছে।
আরো একটা ব্যাপার তার উপন্যাসিকায় আছে যেটা পেছনের আলোচনায় বলতে ভুলে গেছি; হিরো, এন্টিহিরো বা প্রোটাগনিস্টের ধারণা বা ধারা তিনি ভাঙতে চেয়েছেন সম্ভবত। সেকারণেই হয়তো সাপলুডুতে ওরকম কারো অস্তিত্ব আমরা দেখি না। সলোমনকে প্রোটাগনিস্ট মনে হলেও, সে আসলে তা নয়। সে বড়জোর একটা তুলি। যাকে ব্যবহার করে লেখক নিজের উপলব্ধি এঁকেছেন। মজার ব্যাপার এই যে, উপন্যাস হাতে নিয়ে আমরা প্রথমেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করি মূল বা খল চরিত্রকে। সেলিম মোরশেদের সাপলুডু আমাদের এ প্রথাগত খায়েশ পূরণ করে না। সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখি, এ উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য তিনটি- অরৈখিক বয়ান, গল্পহীন উপন্যাস, কোনো প্রোটাগনিস্ট নেই।
লেখকের গল্প নিয়ে বোধহয় আমার কিছু বলা উচিত। কেননা গল্প প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আছে লেখককে জানানোর। তার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ বইটি পড়েছি, কিন্তু সার্বিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ভাল লাগেনি। কেবল সুব্রত সেনগুপ্ত, নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো, কান্নাঘর গল্পগুলো টেনেছে আমাকে।
সুব্রত সেনগুপ্ত গল্পের কথা বলতে গেলে বলবো, এমন রিপোর্টিংয়ের ঢংয়ের গল্প এর আগে পড়িনি। এজন্যেই হতে পারে পছন্দ হয়েছে। এছাড়া, ভালো লেগেছে যে এক চিরন্তন বোধ উঠিয়ে এনেছেন গল্পকার। বোধটা হলো- মানুষ জীবনে যা করে, যে অতীত ফেলে আসে পেছনে তা বর্তমানে নিরাসক্ত চোখেই সাধারণত দেখে মানুষ। সুব্রতও ফেলে আসা কর্মকে নিস্পৃহ হয়ে দেখে। কোনো তাপ-উত্তাপ নেই যেন তার। এ দেখায় যদিও মিশে আছে হাহাকার, শূন্যতা, অতৃপ্তি; তবু ফেলে আসা জীবনের প্রতি নিরাসক্তিই সব ছাপিয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এমনতর নিরাসক্তি এক দিক থেকে বর্তমান মেনে নেয়ার ক্ষমতাটা দেয়, গ্লানি থেকে বাঁচায়। কেননা মানুষ তো ফিরতে পারে না ফেলে আসা সময়ে, বদলাতে পারে না অতীত এবং অতীতের এঁকে আসা পথ ধরে যে বর্তমানে সে দাঁড়িয়ে তা-ও বদলানো সম্ভব না মানুষের পক্ষে। তাহলে আফসোসের চেয়ে নিরাসক্তিই যৌক্তিক? সে কারণেই হয়তো সুব্রতকে নির্বিকার দেখি আমরা।
মেদহীন গল্প নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। ম্যাজিক রিয়েলিজমের কাজটা বেশ ভালো এ গল্পে। লোকেরা যখন নিজেদের চোখ হারিয়ে উল্টো-পাল্টা ভুলভাল চোখ নিজেদের চোখে লাগায় তখন আমি আসলে দেখি, লেখক কী অবলীলায় পাঠককে এক প্রবল ঝাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছেন! সেলিম মোরশেদ, এ গল্পের জন্যে আপনাকে সালাম। অন্যের চোখে নিজেকে দেখতে শুরু করলে আমরা.... আধুনিক সভ্যতার গর্বে গর্বিত ও মুগ্ধ উন্নত-রুচিশীল-বুদ্ধিমান-বিবেকে ভরপুর মানুষেরা যে উদোম হয়ে পড়বো, এ চমৎকার সত্য গল্পে তুলে আনায় আপনার জন্যে দোয়া- আরো আরো অধরা সত্য ধরা দিক আপনার কলমে।
‘কান্নাঘর’ গল্পটাও চমৎকার। অতিভাবনা আর আত্মকথনের বাড়াবাড়ি বাদ দিয়ে গল্পটার মূল মেসেজে আগ্রহ আমার। গল্পে গল্পকার কখনোই বলবেন না তার বক্তব্য কী। তা ধরতে হয় আমাদের। এ গল্পের মেসেজটা আমার কাছে ধরা দেয় এভাবে- ভগবেনেদের নেতা বিজয়মোহন যখন গল্পের ক্লাইম্যাক্সের সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত; যখন শেষমুহূর্তেও তার সমস্ত স্থৈর্য-ব্যক্তিত্ব ও চোখে জল আনার চমকপ্রদ গুণ সব তছনছ হয়ে যায় অক্ষমতায়; তখন পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়, লেখক একটা পথ আঁকছেন। সে পথ এতই স্পষ্ট যে, চোখে না দেখেও তা জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে। সে পথ নেতার। সে পথে হাঁটার যোগ্যতা কেবল তারই যে শেষতক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর পতনের ভাবনাটাও মনে আনে না। সে-ই নেতা যে লড়ে জেতার জন্যে; যে মরিয়া, যে সংকল্পবদ্ধ, যে ছাড়ে না ময়দান। পুলিশ আসার আগে যশোদা যখন দীক্ষার সুতো নিয়ে পা বাড়ায় নিত্যানন্দের দিকে তখন স্পষ্ট হয়ে যায় মানুষের এক আদিম প্রবৃত্তির চিত্র। শক্তিমানের শিষ্যতা বরণের প্রবৃত্তি। মানুষের আদিম এ প্রবৃত্তি তার দিকেই ঝোঁকে, তারই শিষ্যতা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে- যে ভাবুক নয় দুর্বল নয়, যে পরাজয় মানে না, ভাঙে না। শক্তিমান ও বিজয়ীর প্রতি পৃথিবীর সব মুহূর্তেই মানুষ তাকিয়েছে আশা নিয়ে, সামনেও তাকাবে- এ বৈশ্বিক উপলব্ধি দেয় বলেই গল্পটা স্থান-কালের বৃত্ত ভাঙে আর হয়ে ওঠে সার্থক।
এছাড়া শ্রেষ্ঠ গল্পের মলাটে বন্দী বাকি গল্পগুলো ভালো লাগেনি। এর কারণ, অতি বয়ান বা বলা যেতে পারে অতি দৃশ্যায়ন। গল্পে এত বর্ণনা ভালো লাগে না। এছাড়া, মনে হয়েছে তিনি যখন গল্পগুলো লিখেছেন আনন্দ নিয়ে লিখেছেন। শব্দ নিয়ে অনবরত তিনি খেলতে ভালবেসেছেন লিখতে গিয়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, গল্প কমপ্যাক্ট হওয়া ভালো। একটা লাইন সরালেও যেন পুরো গল্পটা টলে ওঠে, এমন হলে তবেই গল্প চূড়ান্ত সফল। তাই যেখানে যেখানে বাদ দেয়া যায় সেখানে বাদ দেয়া আবশ্যক। এমনকি যদি মন সায় না দেয় তবুও নিষ্ঠুরের মতো বাদ দেয়াটা জরুরি। পড়তে গিয়ে কখনো যদি মনে হয় লেখক গল্প লিখেছেন মনের আনন্দে, মাথায় তৈরি হওয়া শব্দ-দৃশ্য তিনি আবেগে খাতায় তুলে দিয়েছেন তখন পড়ার আনন্দ হারাই। উচ্ছ্বাস আর আনন্দে যে গল্প লেখা হয় তা পাঠে কেন যেন আনন্দ আসে না। সম্ভবত এ কারণে তার গল্পের চেয়ে বেশি পছন্দ করেছি উপন্যাসিকাটা- ‘সাপলুডু খেলা’। এটা তিনি হৃদয় দিয়ে না, মগজ দিয়েই লিখেছেন।
কোনো লেখকের সামগ্রিক লেখা নিয়ে আলাপ করতে গেলে একটু দ্বিধায় পড়তে হয় সবসময়। সেলিম মোরশেদের মতো একজন লেখক, যিনি প্রায় সমস্তটা জীবন খরচ করে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের পেছনে, তাকে কয়েক পৃষ্ঠার আলাপে ধারণ করা কতটা সম্ভব? কেন ছোটেন এইসব লেখকেরা, কীসের আশায়? এসবের উত্তরে উপলব্ধিতে আসে এটুকুই যে, তারা আসলে কিছু বলতে চান। এ বলাটুকুই লেখকের আনন্দ। প্রাপ্তি। উচ্ছ্বাস। অর্থকড়ি যশ-খ্যাতি না জুটলেও লেখক এ বলার স্বাধীনতাটা চান। এ স্বাধীনতাটুকু মেনে নিলেই যেন মেলে তার সাতরাজার ধন।
সেলিম মোরশেদের লেখা পাঠ অবশ্যই আনন্দদায়ক যাত্রা নয়। আবেগ-ভাবালুতা দূরে রেখে পাঠ করতে হয় তাকে। সেলিম মোরশেদ পাঠে পাঠককে দায়িত্ব নিতে হয়। চাপ নিতে হয়। তার সাপলুডু খেলা যখন পড়তে শুরু করি, তখন পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখে মনে হয়েছিলো বাহ, সহজেই অল্প সময়ে শেষ করা যাবে.... কিন্তু এগোতেই হোঁচট খেয়েছি বার বার। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে ধরতে লেখকের বোধ। কিছু পাতা বার কয়েক করে পড়েছি। ছোট উপন্যাসিকা (শ’ খানেক পৃষ্ঠা মাত্র) শেষ করতে সময় নিয়েছি দশদিন। যদিও পড়ার গতি আমার ভালো, মিনিটে প্রায় তিনশো শব্দ পড়তে পারি। কোরবানির ঈদের আগের রাতে বইটা শেষ করে মনে হয়েছে, এক লম্বা যাত্রা শেষ হলো তবে!
হতে পারে, সেলিম মোরশেদ ভবিষ্যত পাঠকের কথা মাথায় রেখে তার লেখাগুলো লিখেছেন। হতে পারে, সামনে যে সকল পাঠক তৈরি হবে তারা পড়তে পছন্দ করবে তাকে। আমারও লেখক আবিষ্কারে আগ্রহ বলে সব মিলিয়ে তাকে পড়তে ভালো লেগেছে। কিন্তু যেসব নতুন পাঠক তাকে পড়তে চান তাদের জন্যে কী লেখকের কোনো ভাবনা আছে? বর্তমানে প্রতিটা মানুষের জীবনই জটিল। বেঁচে থাকা টিকে থাকার যুদ্ধে পরিবার, চাকরি, ব্যবসা, ধর্ম, আদর্শ, ঋণ, ব্যক্তিগত সুখ-অসুখ, বন্যা, জলাবদ্ধতা, বেকারত্ব, মহামারীতে অর্ধেক বেতন, চিকিৎসা নেই, সড়ক দুর্ঘটনা, পানির দাম বাড়ছে, বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, খাবারের দাম বাড়ছে, নাগরিক নিরাপত্তা রূপকথার পাখি, ক্ষমতার চাপে পিষ্ট জীবন....... এরকম অজস্র বোঝা মানুষের মাথায়।
এত কিছুর পর যখন একজন পাঠক সাহিত্যে মুক্তি খুঁজতে চায় তখন সে মুক্তি চাইতে গিয়ে কেন লেখকের ইন্টেলেকচুয়ালিটির সাথে লড়ার চাপ নেবে? এ প্রশ্নের উত্তর কী লেখক খুঁজবেন? পাঠকের জন্যে যদি লেখায় লেখক কোনো স্পেস না রাখেন তবে পাঠকের প্রতি নিষ্ঠুরতা হয়ে যায়। পাঠকতো আসলে লেখককে পড়তেই চান, তাই এখানে পাঠকের দিকে হাত বাড়ানোর দায় লেখকেরই। লেখক তার আদর্শ থেকে না সরে, তার লেখার প্রথাবিরোধী সমস্ত উপাদান অটুট রেখে পাঠকের শ্বাস ফেলার কিছু জায়গা তৈরি করবেন কোন কৌশলে সেটা শেষতক তিনিই জানেন। অবশ্যই, কৌশল করে পাঠক ধরার কৌশল না করলেও কিছু আসে যায় না। কেননা দু’ক্ষেত্রেই জগত একই রকম থাকবে। বদলাবে না কিছুই!
নোটঃ
সেলিম মোরশেদের সাপলুডু খেলা উপন্যাসে একখানে নিচের অংশটি আছে-
কিঞ্চি আমার একটা কথার সূত্র ধরে হঠাৎ বললো, ‘এপ্রিলকে তুমি নিষ্ঠুর বললে কেন?’
‘এটা একজন ইংরেজ কবির কথা, আর তাছাড়া এপ্রিলের প্রথম দিনটা (পহেলা এপ্রিল) ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে নিষ্ঠুরই মনে হয়।’
‘কেন’, কিঞ্চি জিজ্ঞেস করলো।
‘১৪৯২ সালের পহেলা এপ্রিলে মুসলমানদের খুন করেছিলো খ্রিস্টানরা। সেটিও বড়ো ছিলো না। যদি খ্রিস্টানরা পুরুষোচিত যুদ্ধের নিয়ম মেনে করতো। মূল বিষয়টি হলো, পর্তুগিজ রানী ইসাবেলা ও তার স্বামী খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড এই দুইজন মিলে মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে বলেছিলো, তারা নিরাপদ আশ্রয় হিশেবে স্পেনের গ্রানাডার মসজিদে আশ্রয় নিতে পারে। মুসলমানরা অস্ত্র ফেলে আশ্রয় নিলে তারা পরে তালা আটকিয়ে মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। বহু মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশুর মৃত্যু হয়।’ শুনে চোখ দুটো বড়ো করে দুঃখ প্রকাশ করলো কিঞ্চি।’
এখানে বর্ণিত তথ্যটুকু ভুল। এটা আসলে একটি জনপ্রিয় গল্প। ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, গ্রানাডায় মুসলিমদের পতন হয় ১৪৯২ সালের জানুয়ারির ২ তারিখে। এটা ঠিক যে গ্রানাডায় মুসলিমদের পতনের পরপরই শুরু হয় ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত অত্যাচার, কিন্তু বোকা বানিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলার গল্প বানোয়াট। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে “Truth About April Fool's Day And Muslim Representative Method of Scientific Inquiry” শিরোনামের প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে। অনলাইনে খুঁজলেই এটি ছাড়াও আরো অনেক আলাপ পাওয়া যাবে। এটি লিখেছেন কানাডার গবেষক ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ তারিক ঘাজি।
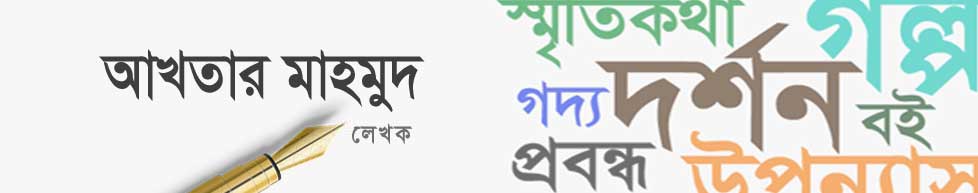

Comments
Post a Comment